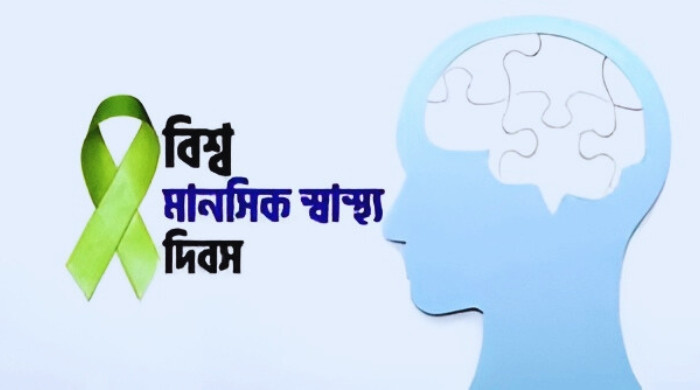
আজ ১০ অক্টোবর, বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস। এ বছরের প্রতিপাদ্য-“Mental health is a universal human right” অর্থাৎ “মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার।” কিন্তু বাংলাদেশে এই অধিকার এখনো কাগজের সীমায় বন্দি। রাজধানীর জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের ওয়ার্ডে গিয়ে দেখা যায়, জায়গার অভাবে রোগীরা মেঝেতে বসে আছেন, কেউ কেউ জানালার পাশে চুপচাপ তাকিয়ে আছেন আকাশের দিকে। পাশেই এক তরুণী কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “আমার মনে হয় কেউ সারাক্ষণ আমার সাথে কথা বলে, কিন্তু কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না।” তার মা নীরবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, বললেন-“আমরা তিন বছর ধরে ঘুরছি। এখানে এলেও ডাক্তার দেখাতে সপ্তাহ লেগে যায়।”
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতি পাঁচজন প্রাপ্তবয়স্কের একজন কোনো না কোনো মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রেও এই হার ১৬ শতাংশের বেশি। কিন্তু চিকিৎসা নিচ্ছেন মাত্র ১৫ শতাংশ মানুষ। সামাজিক লজ্জা, চিকিৎসার অভাব, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা- সব মিলিয়ে মানসিক স্বাস্থ্য এখানে এক নীরব সংকটে পরিণত হয়েছে।
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হলো পাবনা মানসিক হাসপাতাল। ১৯৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই হাসপাতালটি দেশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ মানসিক হাসপাতাল। সরকারি হিসেবে এখানে ৫০০ শয্যা রয়েছে, কিন্তু বাস্তবে ভর্তি থাকে সাত থেকে আট শতাধিক রোগী। শয্যার চেয়ে রোগী বেশি হওয়ায় অনেকেই মেঝেতে ঘুমান। একটি ওয়ার্ডে গাদাগাদি করে ১০-১২ জন রোগী থাকে। হাসপাতালের দেয়াল ভাঙা, ফ্যান বিকল, শৌচাগারের অবস্থা নাজুক। একজন সিনিয়র নার্স জানান, “দুজন নার্স মিলে প্রায় ৬০ জন রোগীকে সামলাতে হয়। অনেক রোগীর পরিবারের কেউই আর খবর নেয় না।” কেউ কেউ এখানে বছরের পর বছর পড়ে থাকেন, কেউবা ভুলে গেছেন নিজের নামও।
শুধু পাবনা নয়, ঢাকার মানসিক হাসপাতালগুলোতেও একই চিত্র। রাজধানীর জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে মানসিক রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বা সাইকোলজিস্টের সংখ্যা খুবই সীমিত। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত সাইকিয়াট্রিস্টের সংখ্যা প্রায় ২৮০ জন, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের সংখ্যা ৪০০ জনেরও কম, অথচ জনসংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি। অর্থাৎ, প্রতি ছয় লাখ মানুষের জন্য মাত্র একজন সাইকিয়াট্রিস্ট।
চট্টগ্রাম মানসিক হাসপাতালে ২০০ শয্যা থাকলেও প্রায় ৩০০ রোগী ভর্তি থাকে নিয়মিত। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের মানসিক বিভাগে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪০০ রোগী আসেন, কিন্তু ডাক্তার আছেন মাত্র তিনজন। খুলনা ও বরিশালে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রায় অকার্যকর। জেলা পর্যায়ে সাইকোলজিক্যাল সার্ভিস বা কাউন্সেলিং সেন্টার নেই বললেই চলে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৫ সালের বাজেটে মানসিক স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ হয়েছে মোট স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ০.৪ শতাংশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন।
এদিকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে। বাংলাদেশে এখনো মানসিক অসুস্থতাকে “পাগলামী” হিসেবে দেখা হয়। কেউ বিষণ্নতায় ভুগলে বলা হয়, “তোদের কিছু হয়নি”, কেউ ভয় বা আতঙ্কে আক্রান্ত হলে বলা হয়, “নাটক করছে।” এই মানসিকতা মানুষকে চিকিৎসা নিতে বাধা দেয়। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শামীমা নাসরিন বলেন, “রোগীরা চিকিৎসা নয়, সমাজের দৃষ্টিকে ভয় পায়। লজ্জা ও গোপনীয়তার কারণে তারা চিকিৎসা নিতে চায় না।”
মানসিক রোগীদের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো তাদের একাকিত্ব। পাবনা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহের হাসপাতালে শত শত রোগী আছেন, যাদের পরিবারের কেউ আর খোঁজ নেন না। কেউ কেউ ১০ বছর ধরে হাসপাতালেই আছেন। পাবনা হাসপাতালের এক বৃদ্ধা বললেন, “আমাকে কেউ দেখতে আসে না। শুধু ওষুধ খাই আর শুয়ে থাকি।” এই দৃশ্যগুলো প্রমাণ করে, মানসিক রোগীদের জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি মানবিক সহানুভূতিও একান্ত প্রয়োজন।
তবে সবকিছুই অন্ধকার নয়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা কিছুটা বেড়েছে। “MonerBondhu”, “Therapy Hub”, “LifeSpring”, “Mind Tale” ইত্যাদি অনলাইন কাউন্সেলিং প্ল্যাটফর্মগুলো এখন শহরাঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য সেল বা কাউন্সেলিং ক্লাব চালু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রিমি রহমান বলেন, “আগে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ কথা বলত না। এখন আমরা বন্ধুদের বলি, তুমি ভালো না থাকলে সাহায্য নাও। এটা এক বড় পরিবর্তন।”
সরকারও ২০২২ সালে ‘ন্যাশনাল মেন্টাল হেলথ পলিসি’ অনুমোদন করেছে, যেখানে জেলা পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ, স্কুলে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও অনলাইন কাউন্সেলিং চালুর পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে, এই পরিকল্পনা এখনো বাস্তবায়নের প্রাথমিক পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। তাদের পরামর্শ, সরকারকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাউন্সেলিং সেন্টার স্থাপন, সাইকোলজিস্ট ও সাইকিয়াট্রিস্ট নিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয় পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য যেন এখনো এক নীরব মহামারির নাম। শরীরের অসুস্থতা আমরা সহজে মেনে নিই, কিন্তু মনের অসুস্থতাকে লুকিয়ে রাখি, অস্বীকার করি, তুচ্ছ করি। প্রতিদিন এই দেশে অসংখ্য মানুষ নিজের ভেতরের অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে- কারও চোখে অশ্রু, কারও মনে অস্থিরতা, আর কারও নিঃশব্দ চিৎকার শোনা যায় না কোলাহলের ভেতরেও। তবু সমাজ তাদের “পাগল” বলে দূরে সরিয়ে দেয়, পরিবার চুপ করে যায়, রাষ্ট্র থাকে উদাসীন। অথচ মানসিক স্বাস্থ্য কোনো বিলাসিতা নয়, এটি টিকে থাকার মৌলিক শর্ত, জীবনেরই অংশ।
বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে তাই প্রশ্নটি আবারও ফিরে আসে- যখন শরীরের জ্বর হলে আমরা তড়িঘড়ি ডাক্তার দেখাই, তখন মনের জ্বর হলে কেন এখনো চুপ থাকি?







